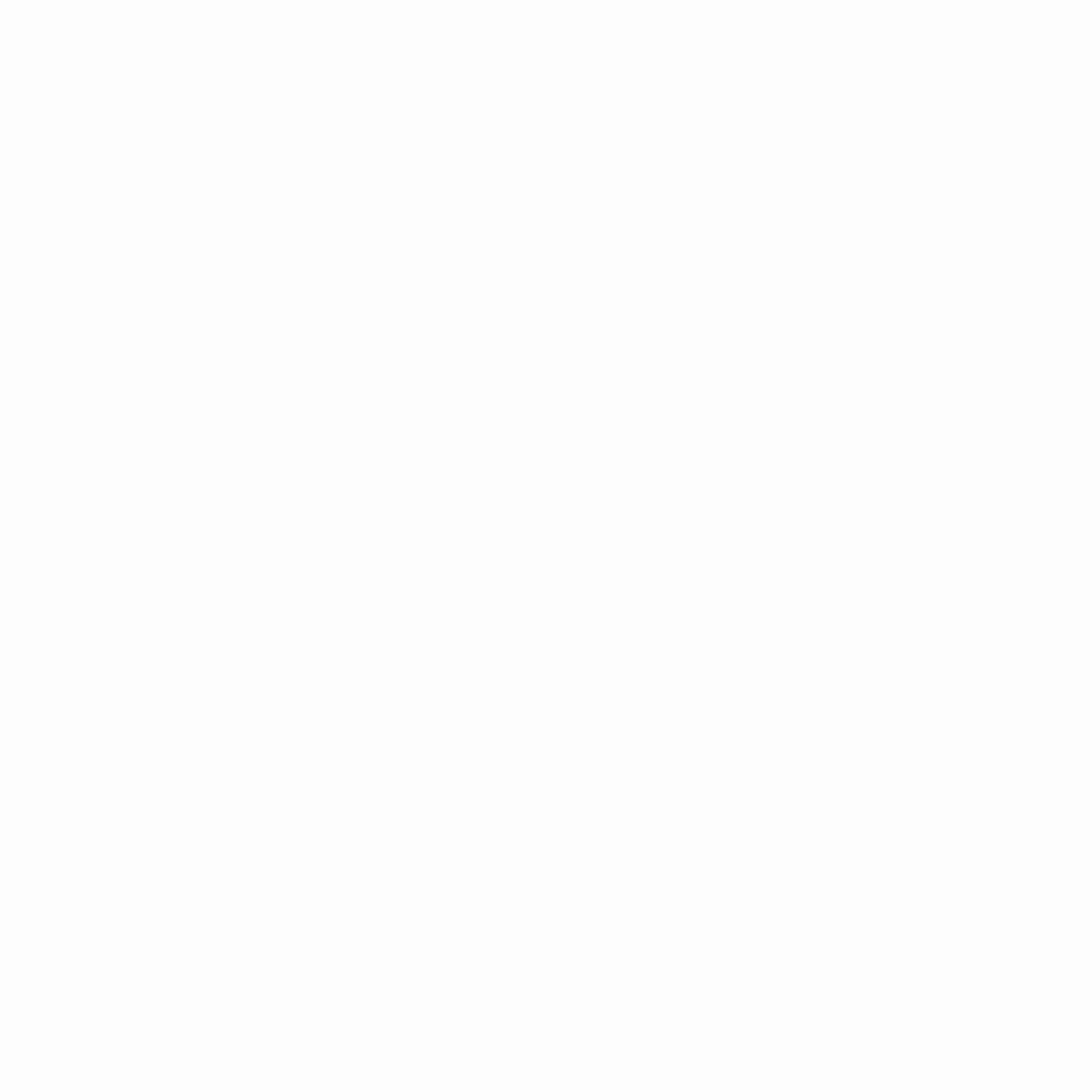জোলা সম্প্রদায়ের কথা শুনলেই মাথায় ঘোরে কবিরের নাম। হিন্দু বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে পরিত্যক্ত হন তিনি। পরবর্তীকালে পালিত হন মুসলমান জোলা দম্পতির কাছে। সাধক কবি চেয়েছিলেন জাতপাত দূর করে ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথতে। ছোট কবিতা বা ‘দোঁহা’ আকারে তিনি বলে গেছেন সে বাণী। তার মূলমন্ত্র ছিল, ‘জন্মের সময় কেউ শূদ্র হয়ে জন্মায় না; নিজেদের পরিচয় নিজেরাই তৈরি করে।’ নিম্নবর্ণের সেই জোলা সম্প্রদায় বাংলার তাঁত শিল্পের ইতিহাসেও পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ছিল তাঁত শিল্পের জন্য সুপরিচিত। ঢাকাই মসলিনের কিংবদন্তি ইউরোপে গীত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলোর একটিতে পরিণত হওয়ায় বাংলা যুক্ত থেকেছে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দূরপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে। আর বাংলার শিল্প ও অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত অনিবার্য নাম জোলা। ফলে প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে জোলাদের ইতিহাস। ব্রিটিশ সার্জন জেমস ওয়াইজ তার লেখা Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal এক্ষেত্রে জরুরি নোকতা হতে পারে। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, ‘অতীতে এরা ছিল অবহেলিত বর্ণের হিন্দু। তারপর কোনো একসময়ে একত্রে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তর হয়েছে সবাই।’
বাংলাদেশের মুসলমান তন্তুবায় পরিচিত ‘জোলা’ নামে। উত্তর ভারতের মুসলমান তাঁতিরাও ‘জুলাহা’ নামেই পরিচিত ছিল। সমুদ্র উপকূলে দেশের অবস্থান ও বাণিজ্যিক কারণে এ অঞ্চলে অধিকতর পণ্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে বর্ণ ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মে শিল্পী-কারিকরদের সমাজে নতুন জাতি ও জাতিশাখা জন্ম নিয়েছে। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার বলেছেন, ‘সুতো কাটার কাজে ও বয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ কারিগরি নৈপুণ্যের তারতম্য অনুযায়ী তাঁতিদের মধ্যে জাতিশাখার সৃষ্টি হচ্ছিল। কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন জাতিশাখার হাতে তৈরি হতে লাগল। তুলো, পেঁজা, সুতো কাটা, সুতোর কুণ্ডলী পাকানো, কুণ্ডলী খুলে সুতোকে আবার কুণ্ডলীর আকার দেয়া, তাঁতে সুতোগুলোকে বস্ত্রের আকার দিয়ে বিন্যস্ত করা, রঙ লাগানো, কাপড়ে ডিজাইনের মুদ্রণ এ-জাতীয় প্রতিটি কাজ স্বতন্ত্র পেশার রূপ নিয়েছিল। কতকগুলো কাজ করত ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলো জাতি। বয়ন শিল্পের সমগ্র প্রক্রিয়া, বিশেষ করে বুননের দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যের বিন্যাস স্বভাবতই অত্যন্ত জটিল কর্ম। অভিজ্ঞতালব্ধ ঐতিহ্যিক নৈপুণ্যের অধিকারী বহু শিল্পী-কারিকর মিলেই কাজগুলো করতে পারত। কাশিম বাজার-মালদা এলাকায় তাফতা বা উজ্জ্বল মোচড়ানো রেশম বস্ত্র, বিভিন্ন রেশম পোকা থেকে তৈরি তসর ও মুগা, হুগলি অঞ্চলের একরঙা রেশমের পটে তৈরি, বিচিত্র সূচিকার্যের নকশি কাঁথা, ঢাকার মসলিনের ওপর একটানা চেইনের ডিজাইনের রেশমি সুতোর সূচিকর্মযুক্ত নকশি কাঁথা বা সুতি বস্ত্রের ঢাকাই চিকন নকশি কাঁথা এবং ঢাকাই মসলিনের সঙ্গে জড়িত বুনন ও শিল্পকর্মের কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে specialisation বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। এই specialisation-এর ভিত্তিতেই জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে কারিকরদের মধ্যে শ্রম-বিভাজন ও শ্রেণীগত মর্যাদার স্তরবিন্যাস তৈরি হয়েছিল।’

পনেরো-ষোলো শতকে লেখা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের দাবি, ম্লেচ্ছ পুরুষের সঙ্গে কুবিন্দক বা তাঁতি নারীর বিয়ের ফলে জোলাদের জন্ম। আবার জোলা পুরুষের সঙ্গে কুবিন্দক নারীর মিলনে উৎপত্তি শরাকদের। এ জাতিশাখাগুলোকে হিন্দু সমাজ কাঠামোর আওতাবহির্ভূত করে দিয়ে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হচ্ছিল। চৌদ্দ-ষোলো শতকব্যাপী শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাণিজ্য বিস্তারের যুগ। আগে মূলত কৃষির দৌরাত্ম্যে কারিকর শ্রেণী অন্ত্যজভাবেই টিকে থেকেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কুবিন্দক বা তাঁতি শ্রেণীর অবস্থানগত ক্রম সৎ শূদ্রের পর্যায়ে। সেখানে তাঁতি জাতির দুটি শাখার নাম শরাক ও জোলা।
মুসলমানদের আগমনের আগে সে যুগের অভিধানকারীরা ধুনরীর কোনো প্রতিশব্দ উল্লেখ করেননি। মুসলিম আমলে সুতি বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন তুলোধোনার কাজ স্বতন্ত্র পেশায় পরিণত হয়েছিল সম্ভবত। পনেরো শতকের শেষ দিকে লেখা বিপ্রদাসের মনসা-বিজয়ে ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে উল্লিখিত মুসলমান জোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী শ্রেণী। তারা সাহিত্যিক উৎসে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। অস্ট্রিক যুগে পেশাজীবীরা সম্ভবত জাতি বা জাতিশাখারূপে বিভাজিত ছিল না। নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে সংগতি রেখে বস্ত্র শিল্প ও বয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ শ্রমিকের ভূমিকা এবং পেশাগত নৈপুণ্যের তারতম্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী ও কারিকর তৈরি হয়েছে। তারাই ক্রমে লাভ করেছে জাতিবর্ণ কাঠামোর পরিচিতি। ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তা অন্যমাত্রা লাভ করেছে। যদিও সে গল্পটা হিন্দুদের ধর্মীয় সাহিত্যে উল্লিখিত হয়নি, কারণ ইসলামে দীক্ষিত পেশাজীবী হিসেবে তখন তারা হিন্দু সমাজের বাইরে অবস্থিত।
ভারতবর্ষে ঘরোয়াভাবে ক্রীতদাস-দাসী কর্তৃক সুতো কাটার ও তুলোধোনার প্রসঙ্গ এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের ১২ হাজার ক্রীতদাস কারিকরের কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ইরফান হাবিব। মোগল আমলে ক্রীতদাসদের বংশধররাও শিল্পজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতিপ্রথাশাসিত কারিকররাও নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে নতুন প্রযুক্তি ও পেশা শিখে নিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত আয়েস-আরামের জন্য দাস নিয়োগ, দাসের সংখ্যাধিক্য এবং দাস ব্যবসা সম্পর্কে আকবরনামা ও বাহরিস্তান-ই-গায়েবি গ্রন্থ এবং ইউরোপীয় পর্যটকদের লেখায় প্রচুর।
ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, সুলতানি আমলে দাসশ্রমের ভিত্তিতে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তারপর মোগল আমল একটি বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভবসংক্রান্ত পূর্বোক্ত প্রকল্পটি ভিত্তিহীন। সুলতানি ও মোগল শাসকরা এবং সেকালের ধনী-সম্ভ্রান্ত লোকজন দাস-দাসীদের কাজে লাগাতেন তাদের বিলাসময় জীবনের আয়েস-আরামের ও জাঁকজমকের প্রয়োজনে। উৎপাদনের কাজে দাসশ্রমের ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। প্রায় সমগ্র ভারতে দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য ছিল। সে পরিস্থিতিতে সহজ প্রক্রিয়ার মাধ্যম কারিকর সংগ্রহ না করে কতকগুলো লোককে দাস বানিয়ে তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দান সম্পর্কিত প্রকল্পটিকে যুক্তিসংগত মনে করেন না মমতাজুর রহমান তরফদার। বরং তার দাবি, বিদেশী ও ধনী বণিকদের কারখানাগুলোয় চড়া হারের মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক কারিকর নিযুক্ত করা হতো। শিল্পজাত পণ্য তৈরি হতো বড় কারখানায় নয়, ঘরোয়া পরিবেশে কতকগুলো পরিবারের লোকজনের হাতে। দাসশ্রমের মাধ্যমে না হয়ে এসব পণ্যের উৎপাদন ঘটত জাতিপ্রথাশাসিত বৌদ্ধ-হিন্দু-জৈন কারিকর-শিল্পী ও তাদের ধর্মান্তরিত বংশধরদের দ্বারা। মুসলিম শাসনের প্রথম দিকের মুদ্রাঙ্কন, কাগজ তৈরি প্রকৃতি কয়েকটি কাজ বাদ দিলে অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে ভারতীয় কারিকরদের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। সামান্য প্রশিক্ষণের সাহায্যে এবং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্যিক কারিকররাই উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারত। জাতি-বর্ণ-শ্রেণী ব্যবস্থার কল্যাণে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শ্রেণীগুলোসহ অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোকজন প্রশিক্ষণ নিয়ে শিল্প-কারিগরি পেশায় যোগ দিত বলে মনে করার সংগত কারণ আছে।

বর্ণ ব্যবস্থার কারণে কতকগুলো জাতির অবনমন বা জাতিভূতি ঘটছিল এবং কতকগুলো অন্ত্যজ-অস্পৃশা জাতির অবস্থান ব্যবস্থার বাইরে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী কোনো এক পর্যায়ে ঠিক এ জাতিগুলোই দেখা যাচ্ছে নবগঠিত মুসলমান সমাজের শিল্পী-কারিকর গোষ্ঠী হিসেবে। ধর্মীয় রূপান্তর সমাজ যে ব্যাপক ইঙ্গিত বিদ্যমান তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে জোলারূপে অভিহিত একটি অন্ত্যজ শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এ শব্দ ফারসি ‘জুলাহা’ শব্দের বিকৃত রূপ। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলার মুসলমান তাঁতিরা ‘জোলা’ নামে পরিচিত। বহু ব্যবহারে ‘জুলাহা’ শব্দের বিকৃতি, সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এ শব্দের সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি পেশাভিত্তিক শ্রেণীর জাতিগত পরিচয় হিসেবে পনেরো-ষোলো শতকে লেখা একটি সংস্কৃত পূরণে ওই শব্দের স্থান লাভ বোধহয় একটি দীর্ঘকালীন সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিণতি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পরিলক্ষিত, জাতি গঠনের পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের ইঙ্গিত বোধহয় প্রচ্ছন্ন। এক্ষেত্রে মমতাজুর রহমান তরফদার দাবি করেন পুরণে উল্লিখিত ‘শরাক’ শব্দটি খুব সম্ভব ‘শ্রাবক’ (বৌদ্ধ) শাব্দর বিকৃত রূপ। ষোলো শতকের শেষ দিকে কবিকত্বণ নিরামিষভোজী শরাক তাঁতিদের জীবজন্তু হত্যা থেকে বিরত দেখেছিলেন। সাম্প্রতিককালেও পুরি ও কটক অঞ্চলের তাঁতিদের বিয়ের অনুষ্ঠানেও বুদ্ধের পুজো করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এ সম্প্রদায়ের তাঁতিদের মদ-মাংস গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে দেখা গেছে।
রাশিকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত জোলা, রংরেজ, সানাকর, হনরী প্রভৃতি পেশাজীবী গোষ্ঠীগুলো ছিল মুসলমান। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর থেকে ইসলামে দীক্ষা নিয়ে এরা বাঙালি মুসলমান সমাজে কারিগরি পেশাজীবী হিসেবে নিজেদের জন্য স্থান করে নিয়েছিল। জুলাহা, রংরেজ, সানাকর, দরজি, কামান (ধনুক), রেস্তা (বেলনা বা মুন্ডর) প্রভৃতি ফারসি শব্দ আলোচনা কারিগরি পেশাগুলোয় মুসলিম প্রাধান্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ পেশাবাচক ও প্রযুক্তিনির্দেশক ফার্সি শব্দগুলো যে হিন্দু সমাজ থেকে ইসলামে দীক্ষিত কারিকর লোকগোষ্ঠীর প্রতিই কালক্রমে প্রযুক্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নেই। নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থার আওতায় কিন্তু তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়েনি। পেশাকে কেন্দ্র করে জাতি-বর্ণভিত্তিক শ্রেণী ব্যবস্থা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নবগঠিত মুসলমান সমাজেও দেখা দিল। সাম্প্রতিককালেও জোলা, রংরেজ, শালকর, ধুনরি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের পেশাগত বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচলিত প্রবাদটি থেকে মুসলমান তাঁতিদের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের ঘৃণাসূচক বিদ্রুপাত্মক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। যেন ভিন্ন ধর্ম থেকে দীক্ষিত জোলা এখনো ইসলামের বিধিবিধান শেখেনি। মুসলমান কারিকর শ্রেণীগুলোর সঙ্গে শিক্ষিত ভদ্র মুসলমানের, এমনকি অশিক্ষিত মুসলমান চাষীর সামাজিক দূরত্ব সহজেই চোখে পড়ে। সাম্প্রতিককালেই লক্ষ করা গেছে, এ দুই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে বিয়েশাদির সম্পর্কের বিরলতা। হিন্দু সমাজে যেমন, মুসলমান সমাজে আনকটা তেমনই কারিকর শ্রেণীগুলো পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মূলত অনার্য জাতিগোষ্ঠী। কেউ কেউ নিম্নবর্ণের হিন্দু হলেও বড় অংশ ছিল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। পেশার দিক থেকে তারা জড়িত ছিল খেতমজুর, দিনমজুর, জেলে, তাঁতি, নাপিত প্রভৃতির সঙ্গে। কেউ উচ্চ পদ পাওয়ার লোভেও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসলাম ও স্থানীয় সংস্কৃতির একটা মিশেল ঘটেছিল নয়া জীবন ব্যবস্থায়। রামাই পণ্ডিত থেকে ফকির গরিবুল্লাহ পর্যন্ত সাহিত্যিক দলিলে বাংলায় ধর্মীয় সমন্বয় প্রচেষ্টার গভীর প্রবণতা দেখা যায়। স্পষ্ট হয় পুঁথি সাহিত্যেও, যেখানে ইসলামী উপাদানের সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে যুক্ত হয়েছে লোকজ বিশ্বাস ও আচার। জীবনযাপনের তাগিদে সমাজের নিচুতলায় থাকা মানুষ সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধবাদ নিয়ে সে অর্থে মাথাব্যথা দেখায়নি। জোলা সম্প্রদায় নিয়ে চর্চার ক্ষেত্রে বিষয়টি সবার আগে জরুরি।
কিতাবি ভিত্তি না থাকলেও সামাজিকভাবে শেখ, মোল্লা, কাজী, সৈয়দ, চৌধুরী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমরা বাঙালি সমাজে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। অঘোষিতভাবেই অভিজাতরা ছিলেন ‘আশরাফ’ সম্প্রদায়ভুক্ত; আর সাধারণ মজুর, কৃষক, শ্রমিক মুসলমানরা ছিল ‘আতরাফ’। এখনো ভারতবর্ষের এমন কিছু এলাকা আছে, যেখানে নিম্নবর্ণের বা আতরাফদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের বা আশরাফদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। যদিও শিক্ষার প্রসারের কারণে এ ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসছে। শ্রেণী তালিকায় সে শ্রমিক মুসলমানের তালিকায় রয়েছে জোলা, হাজাম, বেদে প্রভৃতি নাম।
বাংলা প্রাচীনকাল থেকেই তাঁত শিল্পের কেন্দ্র। তাঁতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নানা পেশা। ইসলাম আগমনের পর সে শ্রেণী-পেশার মানুষকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মের সঙ্গে ইসলামের উপাদান মিশে গিয়ে নিজস্ব এক স্রোত তৈরি করে। মঙ্গলকাব্য ও পুঁথি সাহিত্যে তার কিতাবি প্রমাণ। আর জোলা, হাজাম ও বেদেরা হলো সে সমন্বয়ী প্রক্রিয়ার চলমান ফসিল।
সাময়িক হলেও মুসলিম সমাজে যে একটা সামাজিক বৈষম্য তৈরি করে রেখেছে, তার প্রমাণ জোলা শব্দটিকে গালি বা ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার। জোলা-আনসারি-মোমিন (তাঁতি) সম্প্রদায় ভারতীয় মুসলিমদের এরকমই একটি নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী। জোলা সম্প্রদায়ের মানুষ বংশপরম্পরায় মূলত তাঁত কাপড় ও অন্যান্য বস্ত্র বয়নের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বড় একটা অংশ নিম্নমানের তাঁত বস্ত্র বা গামছা বোনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে আধুনিক সময়ে এসে অনেকেই ভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছে।
সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দিক থেকে জোলারা মুসলমান। কিন্তু বাংলার ধর্মীয় ইতিহাস সমন্বয়ধর্মী। অর্থাৎ এখানে ইসলাম প্রবেশের পর স্থানীয় লোকাচারের মিশেল ঘটেছে ব্যাপকভাবে। ফলে পূর্বতন অনেক বিশ্বাস ও আচার থেকে গেছে মানুষের যাপিত জীবনে। জোলা সম্প্রদায়ের মানুষ অমুসলিম রীতি যে ঠিক কতটা মেনে চলে তার আরো কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জোলারা হিন্দুদের নবান্ন উৎসবের মতোই তারা প্রতি বছর অঘ্রাণ মাসের যেকোনো বৃহস্পতিবার পিঠা উৎসব পালন করে। অঘ্রাণ মাসের শেষ শনিবার বিপদমুক্ত থাকার জন্য ওলাবিবিকে স্মরণ করে ভাত ও মাংস (ফতেহা) রান্না করে। কালী পূজার অমাবস্যা রাত্রিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতোই ভাত না খেয়ে পালন করে দিনটিকে। শুধু তাই নয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানের মণ্ডপে এ সম্প্রদায়ের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। এসব থেকে স্পষ্ট তারা পার্শ্ববর্তী হিন্দু সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি। অবশ্য শিক্ষার প্রসার ঘটায় তারা শরিয়তি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রচলিত লৌকিক ইসলামী রীতিগুলো কমতে কমতে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পর্যায় পৌঁছেছে।
জোলা পরিচয়কে সামাজিকভাবে অসম্মানজনক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বছরের পর বছর। পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে তাঁত বস্ত্রের বাজারে তাদের প্রভাবের ক্ষয়িষ্ণুতার গল্প। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ পেশাটাকে ছেড়ে দিচ্ছে। খোদ জোলা পরিচয়ই যখন সংকটের মুখে, তাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস উদ্ধার করা সেখানে সহজ কাজ নয়। তবে এ কথা স্পষ্ট, বাংলায় যে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে; সেখানে স্বতন্ত্র মাপকাঠি জোলা।
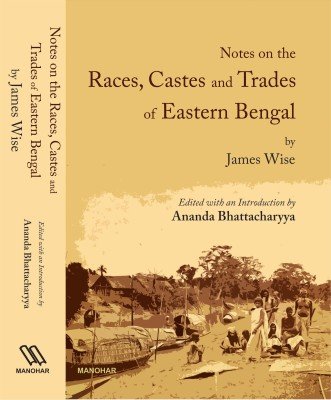
উত্তর ভারতের কবির ছিলেন তাঁতি। আর বাংলার বাউলরাও তন্তুবায় শ্রেণীর লোক। ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের প্রতি কবির ও বাউলদের বিরূপ মনোভাব এবং তাদের মানবিক দরদি দর্শন যেন এ শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। কবিরপন্থী, দাদুপন্থী, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এ প্রতিক্রিয়া ও তাদের পেশার উৎপাদক কারিকর-শিল্পীশ্রেণী এবং ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, করণিক, ভিষক প্রভৃতি উঁচু বর্ণের পেশাজীবী শ্রেণীর মধ্যকার সামাজিক বৈপরীত্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছে। জাতিপ্রথার নঞর্থক দিকগুলো প্রবল। জাতিপ্রথা দ্বারা প্রভাবিত উৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্পী-কারিকরদের মধ্যে পেশাগত নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তির ব্যবস্থা সীমিত থাকত এক-একটি জাতির মধ্যে। ইরফান হাবিব বলেছেন, শ্রমিকের গতিবিধিতে জাতিপ্রথা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি এবং জাতিগুলো তাদের চিরাচরিত পেশা পরিবর্তন করতে পারত। যদিও সেদিক থেকে মমতাজুর রহমান তরফদার পুরোপুরি ঐকমত্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু দিনশেষে একটা কথা সত্য। জোলা সম্প্রদায় বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক স্বীকৃতি সে অর্থে না পেলেও তাদের কাঁধেই ভর করে দাঁড়িয়েছিল একসময় বস্ত্র শিল্পের সমৃদ্ধ জনপদ বাংলা।